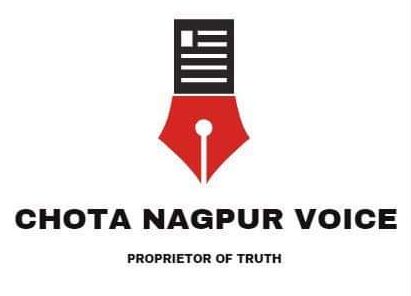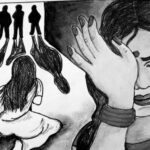সহদেব মাহাত
গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের পরবর্তী স্তরে কৃষিকর্মকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল শ্রম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। ‘শিখ শিখর নাগপুর / আধাআধি খড়গপুর” এই বিশাল ভূখণ্ডে ইতিহাসের পথ ধরে ভাষা ধর্ম সংস্কৃতির বিশাল নিজস্ব পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। ঝাড়খণ্ডি সংস্কৃতি মানেই করম নাচ ও সুরের গুঞ্জরণ, টুসু-বাঁদনার সুরের অনুরণন, ছৌ-পাঁতা-নাটুয়া নাচের দীপ্তিময় পদক্ষেপ, ঢাক-ঢোল-মাদইল-বাঁশির সুরের মূর্ছনা।
ভারতীয় উপমহাদেশের এই বিশাল ভূখন্ডের লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলেন কুড়মি, ভূমিজ, মুন্ডা, রাজোয়াড়, মাল, মাহালি, লোধা, খেড়িয়া, অসুর, বাউরী, হাড়ি, ডোম, মুচি, প্রভৃতি নানান আদিবাসী মানুষেরা। এই এলাকার আদিবাসী মানুষজন কে নিয়ে এক আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। সমাজ তাত্ত্বিকরা যাকে যজমানী ব্যবস্থা নামে অভিহিত করেন। বিভিন্ন পরব-তিহার ও সামাজিক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে শ্রম ভিত্তিক সম্প্রদায়গুলির সাথে ভূস্বামীদের সম্পর্ক তৈরি হত। গ্রামীন অর্থনীতিতে এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে ভূমিকা পালন করত। বংশ পরম্পরাগত বৃত্তি নির্ধারণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করত। তাই, ভূস্বামী ও শ্রমভিত্তিক জনগোষ্ঠীগুলির সাথে সম্পর্ক ছিল একধারে অর্থনৈতিক ও অন্যধারে সামাজিক ও ধর্মীয়।
বৃহৎ ঝাড়খণ্ড তথা ছোটনাগপুর মালভূমির ভূস্বামী পরিবারগুলি ছিল মূলত কুড়মি ও ভূমিজ সম্প্রদায় ভুক্ত। যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠে ছিল তা কুড়মি ও ভূমিজ পরিবারগুলির হাত ধরে। পরবর্তীকালে রাজপুতদের আগমনের ফলে ক্ষমতার রাশ তাঁদের হাতে গেলে দরবারি সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে উঠলেও পুরখেনি সংস্কৃতির রাশ ছিল আদিবাসীদের হাতেই।
করম পরবের আর্থসামাজিক প্রেক্ষপট বুঝতে গেলে আদিম জীবন দর্শন ও বিবর্তনের হাত ধরেই এগোতে হবে। কুড়মি পরিবারগুলিকে ভর করে যে কৃষিকেন্দ্রিক পরব-তিহারগুলির প্রচলন হয়েছিল তার অন্যতম হল করম পরব। করম পরব কৃষি কর্মের সূচনালগ্ন থেকে শুরু হয়েছিল বলে অনেক গবেষক মনে করেন। জাওয়া করম কৃষি কর্মের সূচনার স্মরণ, শস্য ও সন্তান কামনা ও ভাইয়ের মঙ্গল কামনার উৎসব। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে সাড়ম্বরে জাওয়া-করম উৎসব পালন করা হত। জাওয়া ডালি নিয়ে প্রতিদিন রাত হলেই গ্রামে গ্রামে নাচের আসর জুড়ত। এতে যোগ দান করত কুড়মি সহ হিতমিতান সম্প্রদায়ের মানুষজন।
কিন্তু বর্তমানে করম সহ অন্যান্য প্রাচীন পরব তিহার গুলির একটি অবক্ষয় শুরু হয়েছে। নিজস্ব সংস্কৃতিগুলি রক্ষা করতে হলে অবক্ষয়ের কারণগুলো চিহ্নিত করে সেখান থেকে পুনরুত্থানের রাস্তা খুঁজতে হবে।
অবক্ষয়ের কারণগুলো নিম্নরূপ
১) আদিম সংস্কৃতি অবক্ষয়ের মূল কারণ হিসাবে ধরা হয় ‘সংস্কৃতায়ন’কে। শ্রী নিবাসনের মত অনুসারে সংস্কৃতায়ন হল একটি বিশেষ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদিম অধিবাসীরা নিজস্ব নেগ নীতি, ভাষা, ধর্ম, জীবনবোধ, জীবন-প্রণালী পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সমান হওয়ার উদ্যোগী হয়। ব্রাহ্মণদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ অন্ধ ভাবে অনুকরণ ‘করে। কুড়মিরাও তাঁদের অলৌকিক, উদ্ভট, অবাস্তব, বিভেদকামী, অবৈজ্ঞানিক, কল্পকাহিনির মোহজালে পড়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে। কুড়মিরা না পারল হিন্দু হতে না পারল আদিম সংস্কৃতিকে বাদ দিতে। এক জগাখিচুড়ি অবস্থা তৈরি হল। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে কুড়মিদের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের শুরু হয়।
২) গ্রামীন অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার ফলে যজমানী ব্যবস্থায় শিথিলতা দেখা যায়। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে।
৩) শিল্পায়ন, নগরায়ন, আধুনিকীকরণ প্রভৃতির বিকাশ ও বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে আদিম সংস্কৃতি হীনবল হয়ে পড়ে।
৪) শিক্ষার বিস্তারের ফলে আধুনিকতাকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে প্রাচীন সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে।
৫) পেশাগত সম্প্রদায়গুলির পরিষেবার দিন ফুরিয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি শ্রমিক সাপ্লাই কারখানায় পরিণত হয়েছে। ফলে নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে চর্চার সময় নাই।
৬) মানুষের সমাজ সভ্যতা ও জীবনধারার পরিবর্তন হওয়ার ফলে সংস্কৃতির অবক্ষয় শুরু হয়েছে।
৭) আধুনিক কালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে সমাজে ধর্ম বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান গুরুত্ব হারিয়েছে।
সময়ের সাথে সাথে এই এলাকার মানুষ স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। ফলে সরকারী ভাবে প্রাচীন সংস্কৃতি রক্ষায় কিছু কিছু পদক্ষেপ নজরে পড়ছে। আমাদের সমাজের মানুষকে নিজের শেকড়কে অনুধাবন করতে হবে। পরিযায়ী সংস্কৃতির খোলস মুক্ত হতে পারলেই নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা করা সম্ভব।